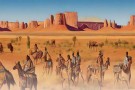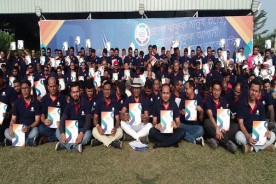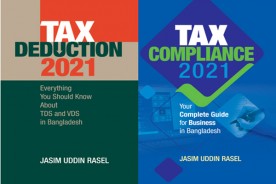- হোম
- কোভিড-১৯: অর্থনৈতিক প্রভাব
আপডেটঃ ২০২৬-০১-৩১ ০০:৩৬:০৮
কোভিড-১৯: অর্থনৈতিক প্রভাব

জসীম উদ্দিন রাসেল
গ্রাম থেকে মানুষ কাজের সন্ধানে শহরে আসে। আর এবার করোনাভাইরাস মহামারি আকারে দেখা দিলে মানুষ শহর ছেড়ে আবার গ্রামমুখী হতে শুরু করেছেন। মানুষ দুবেলা তার পরিবারকে নিয়ে খাবারের জন্য একবার শহর, আরেকবার গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোথাও মানুষ খাবারের নিশ্চয়তা নাই।
কারণ যে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে মানুষ গ্রামে চলে যাওয়ার খবর এসেছে, সেই রিপোর্টেই তাদের ইন্টারভিউ এসেছে, তারা গ্রামে চলে যাচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা কী করবেন তা তারা জানেন না।
তবে তারা কেন গ্রামে যাচ্ছেন? যেখানে নিশ্চয়তা নেই, সেখানে মানুষ কেন ছুটছেন?
এর কারন হলো, বাসা ভাড়া। মাস গেলেই আয়ের বড় একটি অংশ চলে যায় বাসা ভাড়ায়। তারপর যা থাকে তা দিয়ে কোনো রকমে দিন পার করেন। রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা শহরের অলি-গলিতে অসংখ্য টু-লেট ঝুলছে।
আর আগে বহুবার রিপোর্ট বেড়িয়েছে, বিশ্বের মধ্যে ঢাকা শহর থাকার জন্য একটি অযোগ্য শহর। কিন্তু সেই বাস অনপযোগী শহরই আবার বিপরীত দিক থেকে সবচেয়ে ব্যয়বহুল। আর এজন্যই মানুষ হিমশিম খায়।
খেটে খাওয়া মানুষ যেমন বিপদের মধ্যে পড়েছে আবার তেমনি বিপদে পড়েছে যারা ঋণ নিয়ে বাড়ি বানিয়েছেন বা ফ্ল্যাট কিনেছেন তারা। এখন তারা চিন্তায় আছেন, ফ্ল্যাট কাদের কাছে ভাড়া দিবেন। কিভাবে সামনে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করবেন।
এইগুলো যেমন আলোচনা হচ্ছে আবার তেমনি সমালোচনা হচ্ছে, বাসা খালি থাকলেও বাড়িওয়ালারা ভাড়া এক টাকাও কমাবেন না।
আবার কেউ কেউ বলছেন, ২৬ মার্চ থেকে আমাদের দেশে লক ডাউন শুরু হয়েছে। আমরা তিন মাসও নিজেদের জমানো টাকায় চলতে পারলাম না। আমরা এমন ফতুর জাতি হয়ে গেলাম।
এসবই বিক্ষিপ্তভাবে মানুষের মতামত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে জানিয়েছেন।
অনেকেই আবার অতীত স্মৃতি সামনে এনে আফসোস করেছেন। তারা বলছেন, আগে মা-দাদিরা যখন রান্না করতেন তখনও তারা এক মুষ্টি চাল আলাদা করে সঞ্চয় করতেন। যদি কখনো টান পড়তো তখন সেখান থেকে রান্না হতো।
আর এখন ক্রেডিট কার্ডের দুনিয়ায় মানুষ ইএমআই সুবিধা নিয়ে দেশের বাইরে বা দেশে ঘুরতে যায়। নিজের যে একটা পৈতৃক ভিটা আছে তার কথা মনে থাকে না। সেখানেও যে বেড়ানো যায়, এই কথা তাদের মাথায় আসে না।
আসলে বিপদে পড়লে তখন মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের কথা আসে। সব সময় মানুষ যদি হিসেব করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতো তাহলে আমাদের কোনো সমস্যাই থাকতো না।
তবে কিছু ক্ষেত্রে মানুষ নিরুপায়। ইচ্ছা থাকলেও করতে পারেন না।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিটা মানুষের তাদের মাসিক বা বাৎসরিক আয়ের ১০% সঞ্চয় করা উচিত। একটা জরিপে দেখা গেছে ২৭% মানুষ তাদের আয়ের ১০% এর কম সঞ্চয় করেন।
কেন তারা সঞ্চয় করতে পারছেন না?
এর উত্তরে তারা বলেন, দৈনন্দিন খরচ, বাচ্চাদের পড়ালেখার খরচ, ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে তারা আর সঞ্চয় করতে পারছেন না।
এখন হয়তো বলবেন, মানুষ অকারণেও অনেক খরচ করে। বিলাসিতা করে। যেমন, কেউ কেউ বলছেন, আয় অনুযায়ী মানুষ যে এলাকায় থাকতে পারবে সেখানে না থেকে তার থেকে বেশি টাকা ভাড়া দিয়ে থাকবে। পালা করে দামি রেস্তোরায় গিয়ে খাবে।
এখন এগুলো মানুষের মনের ব্যাপার। অনেক সময় মন চায়, একটু ভালো জায়গায় থাকতে, ভালো জায়গায় প্রিয় মানুষগুলোকে নিয়ে খেতে। অনেকেই হয়তো এই মনের চাওয়াগুলোকে ঠিকমত লাগাম টেনে ধরতে পারেন না। আর এজন্যই আর্থিক টানাটানির মধ্যে পড়েন।
তবে সবচেয়ে বেশি টানাটানির মধ্যে থাকেন যারা দৈনিক ভিত্তিতে আয় করেন তারা। যেমন, পরিবহন সেবা খাতের সাথে জড়িত বা ভাসমান কাজে নিয়োজিত শ্রমিক।
পরিবহন খাত
কাজে গেলে টাকা আছে। না গেলেই নাই। দিনের টাকা দিনেই পেয়ে যান। কোনোদিন বেশি পান। কোনোদিন কম পান। এই দিয়ে তারা বাসায় ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে আসেন। পরিবারের লোকজন নিয়ে খেয়ে রাত পার করেন।
আবার পরের দিন ঘুম থেকে উঠে কাজে চলে যান। এভাবে দিনের পর দিন তাদের সংসার চলছে। কোনোদিন বেশি টাকা পেলে বাজার একটু ভালো করে ভালো খেতে চান। কিন্তু টাকা জমিয়ে রাখার চিন্তা মাথায় আসলেও গুরুত্ব দেন না। তারা মনে করেন, এই টাকা জমিয়ে কবে কী হবে?
এজন্য ২৬ মার্চ থেকে লক ডাউন শুরু হলে সবার আগে তারাই বিপদে পড়েন। এসময় অনেকেই বলেন, রাস্তায় প্রতিদিন পরিবহন খাতে বিভিন্ন ধরনের চাঁদা তোলা হয়। সেই টাকা শ্রমিকদের নাম করে তোলা হয়। সেই টাকা কোথায়? এখন শ্রমিকদের দরকারের সময় তাদের কল্যাণে কেন কাজে আসছে না?
তবে দিন এনে দিন খাওয়া এই পরিবহন খাতের নাজুক অবস্থার চেয়ে সবচেয়ে অভিজাত পরিবহন খাত এয়ারলাইন্স আরো নাজুক হয়ে যায়। তাদের আভিজাত্য শেষ হয়ে যায় নিমেষেই। ইওরোপ-আমেরিকার বড় বড় এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলো সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা চাচ্ছিলো প্রথম থেকেই।

পাইলটদের বিনা বেতনে চাকরি চালিয়ে যেতে বলে, আবার কিছু ক্ষেত্রে কর্মীদের ছাঁটাইও করে। সাধারণ মানুষতো পড়ালেখা করা শিক্ষিত না। যেখানে বড় বড় কোম্পানির অনেক অভিজ্ঞ লোক থাকে তাদের কেন এই অবস্থা হলো?
কর্পোরেট সেক্টরের একটা স্ক্যান্ডাল আছে, যখন মুনাফা অনেক বেশি হয় তখন তারা বছরে বড় আকারের বোনাস নিয়ে থাকেন, দেশে-বিদেশে কর্মীদের অফিস থেকে ভ্রমণে পাঠানো হয়। বেহিসেবী অনেক খরচ তখন তারা করেন। তারাও খরচের লাগাম টেনে ধরতে পারেন না। আর এজন্যই কয়েক মাসের মধ্যেই কোম্পানিগুলো দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার অবস্থায় চলে যায়।
কিন্তু এর পালটা উত্তর হিসেবে কেউ কেউ যুক্তি দেবেন, ব্যবসায়ে কেউই নগদ টাকা অলসভাবে ফেলে রাখেন না। সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য থাকে সর্বোত্তম ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট। তাহলেই রিটার্ন ভালো আসবে। আর এজন্যই ব্যবসা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন ব্যবসাগুলো নগদ টাকার ক্রাইসিসে পড়ে যায়।
দুই বেলা খাবার নিয়ে মানুষ যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে চলছে তখন জানা যায়, ধান-চালে নতুন মজুতদারের ফলে দাম বেড়ে গেছে। এর কারণ হিসেবে বলছেন, শহরে এখন টাকা খাটানোর খাত নেই। তাই তারা এখন গ্রামে গিয়ে ধান-চাল মজুত করছেন। এর ফলে বেড়ে গেছে চালের দাম।
দিন এনে দিন খাওয়া মানুষের সঞ্চয় একবারে না থাকলেও যারা চাকরি করেন তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু যারা গার্মেন্টসে চাকরি করেন তাদের বেতন খুবই অল্প। তারা নিজেরা চলে যা থাকে তা বাড়িতে পাঠান। সেই টাকা দিয়ে দুই জায়গায় চলে তাদেরও তেমন কিছু থাকে না।
পোশাক খাত
২৬ মার্চ যখন লক ডাউন শুরু হয় তখন প্রথমবারের লক ডাউন শেষ হতে না হতেই পোশাক মালিকরা তাদের ফ্যাক্টরি খোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শ্রমিকরা টানা ছুটি পেয়ে বাড়ি চলে যান। তারা আবার যে যেভাবে পারেন কাজে ফিরে আসেন।
তখন অনেকেই বলেছেন, পেটের দায়ে নিরুপায় শ্রমিকদের সাথে এমনটা করা হচ্ছে। কিন্তু পোশাক মালিকরা প্রথম থেকেই বলে আসছেন, বিদেশি ক্রেতারা সব অর্ডার বাতিল করে দিচ্ছে। তাদের পক্ষে বেতন দেয়া বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। যেহেতু দেশের রপ্তানির সিংহভাগ পোশাক খাত থেকেই আসে, তাই সরকারও চায় এই খাত যাতে কোনো বিপদে না পড়ে।

তাই সাথে সাথেই এই খাতের জন্য বড় অংকের অল্প সুদে প্রণোদনা ঘোষণা করে। সেখান থেকে ঋণ নিয়ে বেতন দেয়া হয়। পোশাক কারখানাগুলোতে কাজ চলছে। কিন্তু অর্ডার পর্যাপ্ত না। তাই তারা সরকারের কছে আরো টাকা চাইছেন।
কিন্তু কেউ কেউ সমালোচনা করছেন, পোশাক রপ্তানি করে তার ওপর নগদ প্রণোদনা পাওয়া যায়। তার সুবিধা শুধু মালিকরা কেন ভোগ করছেন। শ্রমিকরাও তো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে। তাহলে তাদেরটা কোথায়?
আরেকটা পয়েন্ট তুলছেন, সেটা হল শ্রমিক আইনে, ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড জমা হয়। সেখানে প্রতি বছর কোম্পানি এবং সরকারের ফান্ডে নির্দিষ্ট হারে টাকা জমা হয়। সেই টাকা কোথায়? এখন বিপদের সময় সেই জমানো টাকা কেনো শ্রমিকদের কল্যাণে কাজে লাগানো হচ্ছে না?
পোশাক খাত যেমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বড় ভূমিকা রাখছে, তেমনি প্রবাসী শ্রমিকরাও অনেক বড় অবদান রাখছে।
প্রবাসী শ্রমিক
পোশাক খাতের পাশাপাশি অন্যান্য রপ্তানি খাতও সরকারের কাছ থেকে নগদ সহায়তা পেয়ে থাকে। কিন্তু প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশাল অবদান রাখলেও তারা অবহেলায় থেকেছেন, এ ধরনের খবর প্রায়ই আমরা মিডিয়েতে দেখি।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত গত বছর থেকে সরকার প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের উপর নগদ সহায়তা দেয়া শুরু করে। এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটা কাজ। এটার জন্য সরকার অনেক ধন্যবাদ পেয়েছে মানুষের কাছ থেকে।
কিন্তু কোভিড-১৯ এর ফলে বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রবাসীরা বিপদের মধ্যে আছেন, এ ধরনের খবর প্রকশিত হয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য কোন অর্থ সহায়তা দেখা যায় নি।
বিভিন্ন দেশে বিশেষত, যেসব দেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেশি ছিল সেসব দেশ থেকে প্রবাসীরা ভয়ে দেশে চলে এসেছিলেন। পড়ে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আর কেউ আসতে পারেননি। এখন আবার কিছু বিমান বিশেষ ব্যবস্থায় চলার পর সেসব দেশে ফিরে যাওয়া শুরু হয়েছে।
বিমান চলাচল বন্ধ থাকার কারণে এবং গণপরিবহন পুরোপুরি শুরু না হওয়ার কারণে পর্যটন খাত মুখ থুবড়ে পড়েছে। এর সাথে রয়েছে হোটেল এবং রেস্তোরা।
পর্যটন, হোটেল এবং রেস্তোরা
পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ, সামাজিক দূরত্ব, প্রতিদিন আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলাতে এখনো অনিশ্চিতই থেকে গেছে মানুষের পছন্দের দর্শনীয় স্থানে মুক্তভাবে বেড়ানো। আর এর ফলে পর্যটন খাতের সাথে যারা জড়িত তারা পুরোপুরি বেকার হয়ে গেছেন।
মানুষ যেহেতু বাসায় বন্দি তাই বাইরে বের হয়ে রেস্তোরায় খেতে যাওয়াও একদমই নেই। তাই এই ব্যবসার সাথে যারা আছেন তারাও বসে আছেন।
তবে সীমিত আকারে কিছু চলছে। যেমন, অ্যাপসভিত্তিক খাবার ডেলিভারি সেবা চালু থাকার কারণে যেসব রেস্তোরা এসব অ্যাপসের সাথে যুক্ত আছেন তারা কোনো রকমে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এখন মানুষ আর আগের মতো বাইরের খাবার খেতে আগ্রহী হচ্ছেন না।সবাই তাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত।

খাবার বাসায় পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী হোম ডেলিভারির পরিমান বেড়ে গেছে। এটা শুধু আমাদের দেশেই না অ্যামাজন থেকে শুরু করে সব দেশেরই অনলাইন সার্ভিস জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
বাংলাদেশে ডেলিভারি হয়ে থাকে বাইসাইকেল ব্যবহার করে। কয়েকদিন আগে খবর বের হয়েছে, বাইসাইকেলের চাকা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই না, করোনাভাইরাসের কারণে যেমন অনেক ব্যবসা খাতের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে আবার তেমনি কিছু খাতের ব্যবসার অবস্থা উন্নতি হয়েছে।
বাইসাইকেল/মোটর সাইকেল
বাইসাইকেলের অবস্থার উন্নতি হলেও মোটরসাইকেল ব্যবসা হুমকির মুখে পড়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই এই ব্যবসার অবস্থা দ্রুত গতিতে বাড়ছিলো। এবং এর পেছনে সবচেয়ে যে কারণটি হলো পাঠাও, ওভাই, উবারসহ আরো রাইড শেয়ারিং সেবা চালু হওয়া।
এদের আদিপত্য কতোটুকু বেড়েছে তা যারা ঢাকার ফুটপাথ দিয়ে হেঁটেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন। অনেকেই তখন বিরক্ত হয়ে বলতেন, ফুটপাথ দিয়ে আর আমাদের হাঁটার অবস্থা নেই। এখন সব মোটর সাইকেলদের দখলে চলে গেছে।
আর রাস্তার পাশ দিয়ে হনহন করে বিকট শব্দে বাশি বাজিয়ে সাধারন মানুষের কান বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাস্তায় কার আগে কে যাবে, এই নিয়ে এক মোটর সাইকেল আরেক মোটর সাইকেলের প্রতিযোগিতা হতো। এর ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়ছিল।
তবু মানুষ ভয় নিয়ে মোটর সাইকেলে উঠতো। সাধারণ যাত্রীরা আসলে নিরুপায় হয়ে পড়েছে। একে ঢাকাতে গণপরিবহণ সংখ্যা অপ্রতুল। অন্য দিকে সিএনজি মিটারে যাবে না। ইচ্ছে মতো ভাড়া। উবার দিয়ে সবার চলার মতো সামর্থ নেই।
আবার অফিসে ঠিক সময়ের মধ্যে যেতে না পারলে বসের বা মালিকের কথা শুনতে হয়। এসব কারণে মোটর সাইকেলে মানুষ চড়তে বাধ্য হয় । এমন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত আসে যে, মেয়েরাও মোটর সাইকেলে করে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন। সময়ের সাথে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে যায়।
করোনাভাইরাস এসব দৌড় থেকে সবাইকে থামিয়ে দিয়েছে। দিনের পর দিন মানুষ ঘরবন্ধ হয়ে রয়েছে। লক ডাউন শেষ হয়েছে। কিন্তু তারপরও মানুষের অবাধ যাতায়াত শুরু হয়নি। এখনো অনেক কোম্পানির স্টাফরা বাসায় বসে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।
তাই টেক কোম্পানিগুলোর অবস্থা হয়েছে রমরমা। একদিকে যখন অন্যান্য কোম্পানি পথে বসার উপক্রম হয়েছে সেখানে এসব কোম্পানির মালিকরা হয়েছেন রাতারাতি শত শত বিলিয়ন ডলারের অধিকারী । কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। বাকি সব কোম্পানির অবস্থা খারাপ থাকার কারণে অসংখ্য মানুষ বেকার হচ্ছেন। তারা কাজ পাচ্ছেন না।
তাহলে এখন উপায় কি?
জাতীয় সঞ্চয় স্কিম
ইওরোপ-আমেরিকাতে নাগরিকরা সরকারের কাছ থেকে মাসিক ভিত্তিতে নগদ সহায়তা পাচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশে কী অবস্থা?
শোনা গিয়েছে বাংলাদেশে কিছু পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। তবে এ সংখ্যা অপ্রতুল, একথা বলছেন অনেকেই।
এখন তাহলে এ থেকে উত্তরণের উপায় কী?
আপনাদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে, কয়েক বছর আগে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলাদেশের সব নাগরিকের জন্য জাতীয় সঞ্চয় স্কিম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
খুবই ভালো প্রস্তাব।
যতো তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করা যাবে ততো ভালো হবে। কারণ, সরকারি চাকরির আওতায় খুবই কম সংখ্যক মানুষ রয়েছেন। এদের চাকরির পর নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু যারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন সেখানে গুটি কয়েক ছাড়া অবসরকালীন কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই তারা চাকরির পর নি:স্ব হয়েই বাড়ি ফেরেন। শেষ জীবনে অনিশ্চিত সময় পার করেন।
অথচ উপরে কয়েকবার বলেছি, শ্রম আইনের অধীনে ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ড, পরিবহণ শ্রমিকদের কল্যাণে চাঁদা এমন বিভিন্ন সেক্টরে অনানুষ্ঠানিক ভাবে টাকা সংগ্রহ করা হয়।
জাতীয় সঞ্চয় স্কিম চালু করে এমন সব ফান্ডকে এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এবং যারাই কাজ করছেন, চাকরি করছেন তারা সবাই এই ফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করবেন। এবং একটা নির্দিষ্ট বয়স পরে যতোদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিতে সেখান থেকে নগদ সহায়তা পাবেন।
করোনাভাইরাসের পরে আবার যে কোনো মহামারি আসবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আগে থেকেই সুন্দর একটা ব্যবস্থা তৈরি করে রাখতে হবে। এবারের বাজেট ২০২০-২১ এ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের ওপর গুরত্ব দিলে ভালো হতো।
বাজেট ২০২০-২১
১১
জুন ২০২০ জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে। বাজেট আমাদের সবার কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর করোনাভাইরাসের এই মহামারীর সময় বাজেট আমাদের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাজেট থেকেই আমরা জানতে পারি, সরকার আগামী এক বছর আমাদের জন্য কী করবে। করের চাপ বাড়বে না কমবে? এই প্রশ্ন আমরা যারা করদাতা তারা সবাই করে থাকি।
২০১৫-১৬ কর বর্ষের পর ব্যক্তি করদাতাদের কর মুক্ত আয়ের সীমা বাড়েনি। তখন থেকেই আড়াই লাখ টাকা চলে আসছে। প্রতি বছরই যখন বাজেটের সময় আসে তখন বিভিন্ন মহল থেকে করমুক্ত সীমা বৃদ্ধি করার দাবি করা হয়। এর পেছনে যুক্তি থাকে মুদ্রাস্ফীতি, দেশ উন্নত হচ্ছে, পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে আমাদের থেকেও কর হার কম ইত্যাদি।
কিন্তু প্রতিবারই বাজেট পাস হওয়ার পর ব্যক্তি করদাতারা হতাশ হয়েছেন। একদিকে সরকার প্রতি বছরই বাজেটের আকার বাড়িয়ে আসছে, যার কারণে অনেকেই সমালোচনা করেন বাজেট উচ্চাবিলাসী। আর তার প্রভাব পড়ে এসে করদাতাদের ওপর।
এবার যখন করনাভাইরাস মহামারী আকারে রূপ নেয় তখন আবার ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত সীমা বাড়ানোর জোরালো দাবি উঠে। শেষ পর্যন্ত করদাতাদের দুইটি আশা পূরণ হয়। একটি হলো, করমুক্ত আয়ের সীমা বেড়ে তিন লাখ টাকা এবং আরেকটি হলো, কর হার ১০% থেকে কমে ৫% দিয়ে শুরু করার প্রস্তাব করা হয়। এই দুইটি খবরই ব্যক্তি করদাতাকে স্বস্তি দেয়।
কিন্তু একজন করদাতার যদি বিভিন্ন ধাপে আয় হয় তাহলে তার প্রভাব কি পড়ে ইতোমধ্যেই যারা আয়কর নিয়ে কাজ করেন তারা তা দেখিয়েছেন। এ থেকে দেখা যায়, কম এবং বেশি আয় যাদের আছে তারা সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী।
আর মধ্যম আয়ের করদাতারা তুলনামূলক তাদের চেয়ে অনেক কম সুবিধাভোগী। এখন এই নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা চলছে।
আরেকটি খবর সবাই হয়তো ইতোমধ্যেই লক্ষ করেছেন, টিন থাকলেই দিতে হবে আয়কর রিটার্ন। প্রায়ই মিডিয়াতে খবর আসে, টিনধারি আছেন ৫৫ লাখ, কিন্তু রিটার্ন দাখিল করেন ২২ লাখ। আবার টিন নিলেই যেহেতু রিটার্ন দাখিল করতে হয় না তাই অনেকেই উৎসাহবশত টিন নিয়ে থাকেন। পরে জানতে চান, এখন কী করবেন।
এবার বাজেটে যেহেতু এই নতুন প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তাই আশা করা যায় এখন নতুন করে যারা টিন নেবেন তারা ভালো করে ভেবে চিনতে নেবেন।
শুধুমাত্র দুই ধরনের টিনধারী ছাড়া বাকি সবার জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তারা হলেন, করযোগ্য আয় নেই কিন্তু তাকে জমি বিক্রি করতে হবে বা ক্রেডিট কার্ড নিতে হবে। এই দুই ধরনের ব্যক্তি ছাড়া সবাইকেই রিটার্ন দাখিল করতে হবে।
তবে আশার কথা হলো, সরকার প্রান্তিক করদাতাদের কথা চিন্তা করে মাত্র এক পৃষ্ঠার একটি রিটার্ন ফর্ম তৈরির প্ল্যান করছে। যদি তা আসে তাহলে অনেক সহজে এবং কম সময়ের মধ্যেই রিটার্ন পূরণ করে জমা দেয়া যাবে।
এই
করোনাভাইরাসের সময়ে মেলায় গিয়ে নভেম্বর মাসে ভিড়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা সম্ভব হবে কিনা তা এখনো অনিশ্চিত। কারণ এখনও এর প্রাদুর্ভাব কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই বছরের শেষের দিকে ভ্যাকসিন আসতে পারে। তাহলে আয়কর মেলা অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে।
এ থেকে উত্তরণের উপায় ছিল, অনলাইন রিটার্ন দাখিল। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কয়েক বছর আগে আবুল মাল আবদুল মুহিতকে দিয়ে উদ্ধোধন করালেও তা এখনো কার্যকর
হয়েছে কিনা অনেকেই সে বিষয়ে নিশ্চিত নন। আর এবার বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে, ব্যক্তি করদাতা যদি অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করেন তাহলে দুই হাজার টাকা কর রেয়াত পাবেন।
আগে তো অনলাইন রিটার্ন দাখিল সচল করতে হবে। তারপর সুবিধা। তবে এখনো যেই সময় আছে তার মধ্যে চেষ্টা করে দেখতে পারে।
সবার জন্যই বাজেট ২০২০-২১ মঙ্গল নিয়ে আসুক, এই আশা করছি।
সবাই নিরাপদে থাকুন, সুস্থ থাকুন।
ক্যাটেগরিঃ অর্থনীতি,

জসীম উদ্দিন রাসেল
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও লিড ট্যাক্স কনসালট্যান্ট, ট্যাক্সপার্ট

লকডাউনের পর্যায় পেরিয়ে এসেছি : ড. বিজন
ড. বিজন কুমার শীল বিস্তারিত

ইভ্যালি: প্রতারণার উপত্যকা
বিপরীত স্রোত প্রতিবেদন বিস্তারিত

করোনার জালে বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবন
ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী বিস্তারিত

শুভঙ্কর ফাঁকি দেন নি!
মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান বিস্তারিত

কোয়ারেন্টিন জীবনযাপন
যারিন মালিয়াত অদ্রিতা বিস্তারিত

ভি-টিউটর মাইক্রোসফট অফিস স্পেশালিস্ট বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫
মাইক্রোসফট অফিস স্পেশালিস্ট (M.. বিস্তারিত

আজ রোদে গিয়েছেন তো ?
মুস্তাকিম আহমেদ বিস্তারিত

বিরোধী দলের উচিত ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনে উদ্যোগী হওয়া
সাংবাদিক শফিক রেহমানের পুরো বক.. বিস্তারিত

বৈশাখে ইলিশ নয়
উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আ.. বিস্তারিত